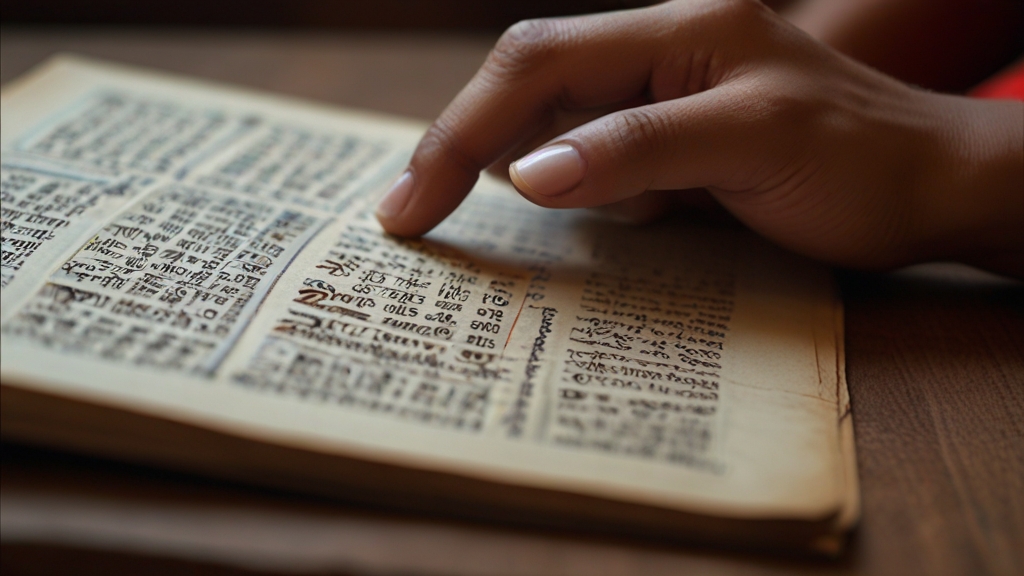ও৩ম্
পূর্ব আচার্য, উপকুলপতি এবং সংস্কৃত বিভাগ অধ্যক্ষ
গুরুকুল কাংগড়ী বিশ্ববিদ্যালয়, হরিদ্বার
পূর্ব প্রোফেসর এবং অধ্যক্ষ, মহর্ষি দয়ানন্দ বৈদিক অনুসন্ধান পীঠ
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়।
ড. আচার্য রামনাথ বেদালঙ্কার বিদ্যামার্ত- কৃত
সামবেদ-সংহিতা
বাংলা ভাষা-ভাষ্য
পূর্বার্চিক (ছন্দ আর্চিক) আগ্নেয় কা- পর্ব বা প্রথম দশতি
অথ প্রথম প্রপাঠক, প্রথমোঽধ্যায়, অথ প্রথমার্দ্ধে
প্রথম দশতি, প্রথম খ- প্রারম্ভ।
বেদ স্বাধ্যায়, বিনিয়োগ, যোজন-যাজনা, স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনার পূর্বে আমাদের মন্ত্রের উপরে চার (ঋষি, দেবতা, ছন্দ আর স্বর) বিষয় সামন্য আর বেদভাষ্য বিষয় পূর্ণ জ্ঞান জানা আবশ্যক।
ঋষিঃ—-প্রাণা বাব ঋষয়ঃ। (শ০ ব্রা০ ৮.৪.১.৫)। প্রাণা ঋষয়ঃ। (শ০ ব্রা০ ৭.২.৩.৫)। এই সম্পূর্ণ মন্ত্রই আকাশ গঙ্গায় ব্যাপ্তির নামই প্রাণ রূপ ঋষি আর প্রাণা কম্পনাৎ। (ব্রহ্ম০ সূ০) ১.৩.৩৯। প্রাণই কম্পন রূপ গতি এবং প্রাণা রশ্ময়ঃ। (তৈ০ ব্রা০ ৩.২.৫.২)। রশ্মিই প্রাণ। ঋষী গতৌ ঋষি নামক প্রাণ এক বিশিষ্ট গতিযুক্ত। এই ঋষি, ছন্দ আর স্বর এর প্রভাবে দেবতা নির্মাণ হয়। এইজন্য ঋষিজ্ঞান মন্ত্রার্থে অত্যন্ত সহায়ক হয়। এই দৃষ্টি দ্বারা প্রাচীন পরম্পরাতে অত্যন্ত আবশ্যক কহিয়াছেন।
নিরুক্তকার য়াস্কমুনি (ঋ০ ১.১০৫.৮) ত্রিত ঋষির (নিরু০ ৪.৬) এবং (ঋ০ ৮.৬৮) সূক্তে জালবদ্ধ সৎস্য ঋষির (নিরু০ ৬.২৭) ইত্যাদি মন্ত্রে অর্থ-করণে সঙ্গতি-ভূমিকা প্রদর্শিত হয়।
আর প্রত্যেক মন্ত্রের পূর্বে ঋষি নামের অর্থ সহিত বেদ মন্ত্র পঠন-পাঠন করা উচিত….বাক্যনিয়মাৎ।। (মীমা০ সূ০ ১.২.৩২০)। অর্থাৎ (বাক্যনিয়মাৎ) বেদে প্রত্যেক মন্ত্রে ঋষির নাম পাইবার কারণ বেদকে অর্থ সহিত পঠন-পাঠন করা উচিত।
দেবতাঃ—-য়াং য়াং দেবতাং নিরাহ তস্যাস্তস্যাস্তাদ্ভাব্যমনুভবতি। (নিরু০ ১৩.১৩) অর্থাৎ যে-যে দেবতার নির্বাচন বা কথন করে, সেই-সেই দেবতার তদ্রুপ ভাবের অনুভতিও সঙ্গে-সঙ্গে হইয়া থাকে। তদ্রুপ অনুভতি সেই দেবতার স্বরূপের জ্ঞান বা আন্তরিক প্রত্যক্ষী করণ করেন। ইহা তদ্রুপ অনুভতিই অর্থের নির্ণায়ক হয়।
ছন্দঃ—-বেদাঃ এব সবিতা ছন্দাংসি সাবিত্রী (গো০ ব্রা০ পূ০ ১.৩৩) অর্থাৎ সব বেদই বিচরণশীল আর ছন্দ [আনন্দকারক কর্ম বা গায়ত্রী আদি ছন্দ] বিচরণশীলের সেবাকারী হয়।
স্বরঃ—-প্রজাপতিঃ স্বরঃ (ষ০ ব্রা০ ৩.৭) অর্থাৎ প্রজাপতিই স্বর। এবং উচ্ছিষ্টে স্বরঃ সাম্নো০ (অথর্ব০ ১১.৭.৫) অর্থাৎ সামের স্বর উচ্ছিষ্ট রূপ ভগবানে সন্নিহিত। ইহা হইতে স্পষ্ট হয় যে সাম মন্ত্রের উপরে স্বরও ভগবান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।
এই চার বিষয় ঋষি, দেবতা, ছন্দ আর স্বর সিদ্ধে শব্দার্থসম্বন্ধে (মহাভাষ্য পস্পশাহ্নিক)। অর্থাৎ শব্দ-অর্থ আর তাঁহার সম্বন্ধ নিত্য। নিত্য শাস্ত্রে কোনও অনিত্য শব্দ থাকিতে পারে না। মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, দেবতা, স্বরঃ লইয়াই একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্র তৈরী হয়। মন্ত্রের ঋষি+ছন্দঃ+স্বরঃ এর দ্বারা দেবতা সিদ্ধ হয়। মন্ত্রে তিন পদার্থ মিলিয়াই দেবতার নির্মাণ করেন। দেবতা হইল মন্ত্রের মূল বিষয়। দেবতা কি-কি বস্তু দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাঁহা ঋষিঃ+ছন্দঃ+স্বরঃ এই তিন বস্তুর প্রভাব দ্বারা তাঁহা জানা যায়। অতএব এই সকল মন্ত্র হইতে আলাদা নহে। যাঁহা মন্ত্র হইতে আলাদা নহে, তাঁহা অনাদি এবং নিত্য সত্তা। সুতরাং অধুনা পণ্ডিতগণ মন্ত্রে ঋষি বিষয়ে যেসব গল্প-গুজব রচনা করেন তাঁহা মিথ্যা এবং অনিত্য জানিয়া পরিত্যাজ্য। এইজন্য বেদ ঘোষণা করিয়াছেন—
বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং য়ৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
য়দেষাং শ্রেষ্ঠং য়দরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।। (ঋ০ ১০.৭১.৩)
অর্থাৎ হে (বৃহস্পতে) বাণীর স্বামী পরমাত্মা (বাচঃ অগ্রং প্রথমম্) বাণীর শ্রেষ্ঠরূপ সৃষ্টির প্রারম্ভে (নামধেয়ং য়ৎ দধানাঃ প্রৈরত) পদার্থ মাত্রের নাম ব্যবহারের প্রদর্শক বেদকে ধারণ করিয়া পরম ঋষিগণ প্রেরিত বা [অন্য ঋষিদের] জানান (য়ৎ) তখন (এষাম্) এই পরম ঋষিদের (শ্রেষ্ঠম্) শ্রেষ্ঠ কার্য (অরিপ্রম্ আসীৎ) পাপ রহিত নিষ্পাপ ছিল (প্রেণা এষাং গুহা নিহিতম্) তোমার [পরমাত্মার] প্রেরণা দ্বারা এই পরম ঋষিগণ হৃদয় গুহাতে নিহিত করেন।
অর্থাৎ এই মন্ত্র দ্বারা জানা যায়-অগ্নি, বায়ু, আদিত্য আর অঙ্গিরা ঋষিগণ জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা মন্ত্রকে দর্শন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন মূল চারবেদ সংহিতার ব্যাখ্যা মন্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত পুরাণ, ইতিহাস, কল্প, গাথা, নারাশংসী, উপনিষদ, শ্লোক, বিদ্যা, সূত্র, ব্যাখ্যান আর অনুব্যাখ্যান পরমাত্মা হইতে প্রকাশিত (অথর্ব০ ১১.৬.১১-১২; শ০ ব্রা০ ১৪.৫.৪.১০; বৃহ০ উ০ ২.৫.১১)। আর পরবর্তীতে বিদ্বানগণ মানবের বেদের ব্যাখ্যা পরম্পরা স্থির রাখিবার জন্য রচনা করিয়াছেন….ব্রাহ্মণানীতিহাসান্ পুরাণানি কল্পান্ গাথা নারাশংসীরিতি (তৈ০ আ০ ২.২.৯) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ গ্রন্থই ইতিহাস, পুরাণ, কল্প, গাথা এবং নারাশাংসী নামে কথিত।
ঋষিঃ-ভরদ্বাজঃ।। মনো বৈ ভরদ্বাজ…..তস্মান্মনো ভরদ্বাজ ঋষিঃ। (শ০ ব্রা০ ৮.১.১.৯) অর্থাৎ মনই ভরদ্বাজ ঋষি। বাজ অন্ন, যাঁহা মন তাঁহাই অন্ন। এইজন্য মন ভরদ্বাজ ঋষি কথিত)।
দেবতা-অগ্নিঃ।। জ্ঞান প্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মা, বিদ্যুৎ, সূর্য, ভৌতিক অগ্নি, সূক্ষ্ম অগ্নি, বিদ্বান, আচার্য ও রাজা ইত্যাদি।
ছন্দঃ-গায়ত্রী।। এতদ্বৈ গায়ত্রী ছন্দ আসীষ্ঠম্ (শ০ ব্রা০ ৮.২.৩.৯) অর্থাৎ এই ছন্দরশ্মি অন্য ছন্দরশ্মি হইতে সূক্ষ্মতম পরন্তু সর্বাধিক তেজস্বী হইয়া থাকে। ইহার গতি সর্বাধিক হইয়া থাকে। সাত ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী ছন্দের গতি বেশী হইয়া থাকে।
স্বরঃ-ষড়জঃ।। বেদের বাস্তবিক অভিপ্রায় পর্যন্ত জাইবার জন্য যত সাধন আছে, তাঁহার মধ্যে স্বর-শাস্ত্র সব চাইতে প্রধান। ব্যাকরণ আর নিরুক্ত যেরূপ প্রমুখ শাস্ত্র ও স্বর-শাস্ত্রকে অঙ্গ করিয়াই বেদার্থ-জ্ঞানে সহায়তা হয়। অধিং স্বরে (ঋ০ ৮.৭২.৭) অর্থাৎ স্বর দ্বারা যুক্ত শব্দাত্মক বাক্।
প্রথম মন্ত্রে অগ্নি নাম দ্বারা পরমাত্মা, বিদ্বান, রাজা আদির আহ্বান।
ঋষিঃ-ভরদ্বাজঃ।। দেবতা-অগ্নিঃ।। ছন্দঃ-গায়ত্রী।। স্বরঃ-ষড়জঃ।।
ও৩ম্। অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি ৰর্হিষি।। ১।।
পদপাঠঃ অগ্নে। আ। য়াহি। বীতয়ে। গৃণানঃ। হব্য। দাতয়ে। নি। হোতা। সৎসি। ৰর্হিষি।। ১।।
[প্রথম] পরমাত্মার পক্ষে–হে (অগ্নে) সর্ব-অগ্রণী, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, সর্বসুখ-প্রদাতা, সর্ব-প্রকাশময়, সর্ব-প্রকাশক গুণাতীত পরমাত্মা! আপনি (গৃণানঃ) [বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের] সমস্ত কর্তব্যের উপদেশ করিয়া (বীতয়ে) আমাদিগের প্রগতি জন্য, আমাদিগের বিচার আর কর্মে ব্যাপ্ত হইবার জন্য, হৃদয়ে সৎগুণ উৎপন্ন করিবার জন্য, স্নেহ করিবার জন্য, আমাদিগের মনে উৎপন্ন কাম-ক্রোধ আদিকে বাহিরে নিক্ষেপের জন্য এবং (হব্যদাতয়ে) দানযোগ্য পদার্থ শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, শ্রেষ্ঠ কর্ম, শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ ধন আদির দানের জন্য (আ য়াহি) আসুন অর্থাৎ প্রাপ্ত হউন। (হোতা) শক্তি আদির দাতা এবং দূর্বলতা আদির বিনাশক হইয়া (ৰর্হিষি) হৃদয়রূপ অন্তরিক্ষে [বা সর্বত্র] (নি সৎসি) [সদা] উপবিষ্ট অর্থাৎ প্রকাশিত ও বিরাজমান।। ১।।
অথবা–(অগ্নে) হে জ্ঞান-প্রকাশ-স্বরূপ পরমাত্মা! তুমি (বীতয়ে) আমার ভীতর তোমার ব্যাপ্তি-প্রাপ্তির জন্য এবং (হব্যদাতয়ে) নিজেকে তোমার দানের জন্য (গৃণানঃ) স্তুতি করিয়া থাকি; (আ য়াহি) আসো-আমার দিকে গতি কর; (হোতা ৰর্হিষি নি সৎসি) আমার অধ্যাত্ম যজ্ঞের হোতা-সম্পাদনকারী ঋত্বিক হইয়া অধ্যাত্ম যজ্ঞের সদন হৃদয় আকাশে, হৃদয়াসনে বিরাজমান হও।। ১।।
অথবা–(অগ্নে) হে জগৎ অগ্রণী অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা! (আ য়াহি) আসুন, প্রকট হউন আমাদের হৃদয়ে, (বীতয়ে) আমাদের উপাসকের জীবনে প্রগতি দানের জন্য, আমাদের সব কার্যে ব্রাপ্ত হইবার জন্য, আমাদের নতুন আধ্যাত্মিক জন্ম দানের জন্য, আমাদের মধ্যে শোভা উৎপন্ন করিবার জন্য, আমাদের দুর্গুণকে পরাস্ত করিবার জন্য, আমাদের পাপকে ভস্ম করিবার জন্য, (গৃণানঃ) আপনি গুরুবৎ উপদেশ করেন, অনাদি গুরু (হব্যদাতয়ে) দান যোগ্য আর ভোগ যোগ্য বস্তু দানের জন্য। (হোতা) আপনি নিজের দিকে উপাসকের আহ্বান করেন, দাতা আর চরাচরের কর্তা। আপনি আমাদিগের (ৰর্হিষি) হৃদয়াসনে (নি সৎসি) নিরন্তর বিরাজমান।। ১।।
বৈদিক সংস্কৃতিতে দৈনিক ব্যবহার তথা বিশেষ সংস্কার, যাগ পর্ব আদিতে বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগ প্রচুর মাত্রায় হইয়া থাকেন। মন্ত্র প্রয়োগের এক বিধি। যদি বিধিপূর্বক মন্ত্রের প্রয়োগ করা হয় তাঁহা হইলে অল্প সময়ে অনেক লাভ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ অনেক মন্ত্রে ঈশ^রের স্তুতি, প্রার্থনা বা উপাসনা হয়। এই স্তুতি আদির ফল বিধিপূর্বক মন্ত্রের প্রয়োগ দ্বারাই প্রাপ্ত হয়, অন্যথা নহে। যেরূপ আমরা এখন বেদ মন্ত্রের ঈশ্বর স্তুতি, প্রার্থনা ও উপাসনার ভাষ্য উপলব্ধ পাই তদ্রুপ ভাষ্য কাম্য নহে।
ঋষিদেব স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী’র অভিপ্রায় নিম্নে এরূপ কাম্য দেখুন––
স্তুতি—(ক) যে ঈশ^র বা কোনও দ্বিতীয় পদার্থের গুণ জ্ঞান, কথন, শ্রবণ আর সত্য ভাষণ করেন, তাঁহা স্তুতি কথিত হয়। (আর্য়োদ্দে০ ২১)।
(খ) স্তুতি গুণকীর্তন শ্রবণ আর জ্ঞান হওয়া। (স্বমন্তব্যা০ ৪৮)।
স্তুতির ফল-(ক) যে গুণ জ্ঞান আদি করার জন্য গুণযুক্ত পদার্থে প্রীতি হয় তাঁহাকে স্তুতির ফল কহিয়া থাকেন। (আর্য়োদ্দে০ ২২)।
(খ) স্তুতির ফল অর্থাৎ যথার্থ বর্ণন, ঈশ্বর স্তুতি করিবার পর নিজের প্রীতি বৃদ্ধি হয়, কেননা তাঁহার যাঁহা-যাঁহা গুণ সামর্থে আসে, তাঁহার-তাঁহার প্রীতি অধিক দৃঢ় হইয়া থাকেন। (উপদেশমঞ্জরী)।
(গ) স্তুতির ফল ঈশ্বরে প্রীতি, উহার গুণ, কর্ম, স্বভাবের ন্যায় নিজের গুণ, কর্ম, স্বভাব সংশোধন করা। (সত্যার্থপ্রকাশ, সপ্তমসমুল্লাস)।
(ঘ) স্তুতির ফল প্রীতি আদি হওয়া। (স্বমন্তব্যা০ ৪৮)।
প্রার্থনা—-(ক) নিজের পূর্ণ পুরুষার্থের পশ্চাৎ উত্তম কর্মের সিদ্ধির জন্য পরমেশ^র বা অন্য কোনও সামর্থ্যবান মানবের সহায়তা লইবার নাম প্রার্থনা কথিত হয়। (আর্য়োদ্দে০ ২৪)।
(খ) প্রার্থনা-নিজের সামর্থ্যরে পশ্চাৎ ঈশ^রের সম্বন্ধ দ্বারা যে বিজ্ঞান আদি প্রাপ্ত হয় উহার জন্য ঈশ^র হইতে যাচনা করা। (স্বমন্তব্যা০ ৪৯)।
প্রার্থনার ফল-(ক) অভিমানের নাশ, আত্মাতে আদ্রতা , গুণ গ্রহণে পুরুষার্থ আর অত্যন্ত প্রীতি হওয়া প্রার্থনার ফল। (আর্য়োদ্দে০ ২৫)।
(খ) নিরভিমান, উৎসাহ বা সহায় (বিজ্ঞান আদির) প্রাপ্তি। (সত্যার্থপ্রকাশ, সপ্তমসমুল্লাস)।
(গ) প্রার্থনা দ্বারা পশ্চাত্তাপ হইয়া থাকে আর সামনের পাপ বাসনার বল ক্ষুন্ন হয়। (উপদেশমঞ্জরী)।
উপাসনা—-(ক) যাঁহা দ্বারা ঈশ^র এরই আনন্দ স্বরূপে নিজের আত্মাকে মগ্ন করিতে হয়, উহাকে উপাসনা কহিয়া থাকেন। (আর্য়োদ্দে০ ২৬)।
(খ) যেরূপ ঈশ^রের গুণ, কর্ম, স্বভাব পবিত্র, তদ্রুপ নিজের করা, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক, নিজেকে ব্যাপ্য জানিয়া ঈশ^রের সমীপ আমি আর আমাদিগের সমীপ ঈশ্বর, এরূপ নিশ্চয় যোগাভ্যাস দ্বারা সাক্ষাৎ করা উপাসনা কথিত হয়। (স্বমন্তব্যা০
৫০)।
উপাসনার ফল-(ক) পরব্রহ্ম হইতে মিল, উহার সাক্ষাৎকার বা জ্ঞানেরউন্নতি। (সত্যার্থপ্রকাশ, সপ্তমসমুল্লাস)।
(খ) উপাসনার দ্বারা আত্মাতে সুখের প্রাদুর্ভাব হয়। (উপদেশমঞ্জরী)।
(গ) যেরূপ ঈশ্বরের গুণ, কর্ম, স্বভাব পবিত্র, তদ্রুপ নিজের করা, ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক, নিজেকে ব্যাপ্য জানিয়া ঈশ্বরের সমীপ আমি আর আমাদিগের সমীপ ঈশ্বর, এরূপ নিশ্চয় যোগাভ্যাস দ্বারা সাক্ষাৎ করা উপাসনা কথিত হয়, ইহার ফল জ্ঞানের উন্নতি আদি। (স্বমন্তব্যা০ ৫০)।
এইজন্য জৈমিনী মুনির সিদ্ধান্ত দেখুন–গুণবাদস্তু।। (মীমা০ সূ০ ১.২.১০)। অর্থাৎ (তু) শব্দ শঙ্কা পরিহারার্থ হয়, (গুণবাদঃ) যে স্তুতিবাদ কথিত হয়, তাঁহা মূলত গুণবাদ।
অর্থাৎ [দ্বিতীয়ঃ] বিদ্বানের পক্ষে। বিদ্বানদিগকেও অগ্নি সম্বোধন করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে বিদ্বান অগ্নি স্বরূপ, যিনি ঋকের সংগ্রহিতা এবং সত্যময় হইয়া থাকেন। (ঋ০ ১.১৪৫.৫) এবং বিদ্বান অগ্নি তুল্য, যিনি বল প্রদান করেন। (ঋ০ ৩.২৫.২) ইত্যাদি মন্ত্র প্রমাণ।
হে (অগ্নে) বিদ্বান! [ঋষি, দেবতা, ছন্দ ও স্বরের প্রয়োগ বিধি জানিয়া] (গৃণানঃ) যজ্ঞবিধি এবং যজ্ঞের উপকার রহস্যের উপদেশ করিয়া আপনি (বিতয়ে) যজ্ঞে প্রগতি দানের জন্য এবং (হব্যদাতয়ে) হবন সামগ্রীকে যজ্ঞাগ্নিতে প্রদানের জন্য (আ য়াহি) আগমন করুন। (হোতা) হোমের সম্পাদনকারী হইয়া (ৰর্হিষি) কুশাসন অর্থাৎ তৃণসদৃশ দ্বারা নির্মিত [বা শুদ্ধ পরিস্কার] যজ্ঞাসনে (নি সৎসি) আসীন হউন। এই প্রকার আমাদিগের যজমান যজ্ঞকে নিরাপদে সঞ্চালিত করুন।। ১।।
অর্থাৎ [তৃতীয়ঃ] রাজার পক্ষে। রাজাদিগকেও অগ্নি সম্বোধন করা হয়। ইহার মধ্যে হে নায়ক! তুমি প্রজা পালক, উত্তম দানী, প্রজার রাষ্ট্রগৃহে রাজা রূপে অলঙ্কৃত কর। (ঋ০ ২.১.৮) রাজা অগ্নি তুল্য, যিনি রাষ্ট্ররূপ গৃহের অধিপতি এবং রাষ্ট্র যজ্ঞের ঋত্বিক হইয়া থাকেন। (ঋ০ ৬.১৫.১৩) ইত্যাদি মন্ত্র প্রমাণ।
হে (অগ্নে) অগ্রনায়ক রাজন! আপনি (গৃণানঃ) [বেদানুকূল] রাজ নিয়মকে ঘোষিত করিয়া (বীতয়ে) রাষ্ট্রের প্রগতি দানের জন্য, নিজের প্রভাব [বেদানুকূল সামর্থ্য] দ্বারা প্রজাদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইবার জন্য, প্রজাদিগের মধ্যে রাষ্ট্র-ভাবনা এবং বিদ্যা, ন্যায় আদির উৎপন্ন করিবার জন্য তথা [বুদ্ধিরূপ] হৃদয়জাত এবং বাহ্য শত্রুদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য এবং (হব্যদাতয়ে) রাষ্ট্র-কল্যাণের জন্য দেহ, মন, রাজকোষ আদি সর্বস্বকে হবনীয় স্বরূপ হইয়া সমাজ কল্যাণার্থে উৎসর্গ করিবার জন্য (আ য়াহি) প্রত্যাগমন করুন। (হোতা) রাষ্ট্র-যজ্ঞের [বেদানুকূল সর্ব প্রকারের] সম্পাদক হইয়া (ৰর্হিষি) রাজ-সিংহাসন বা রাজ-সভাতে (নি সৎসি) উপবিষ্ট হইয়া [অলঙ্কিত করুন]।। ১।।
অথবা–হে (অগ্নে) প্রকাশ পুঞ্জ! (বীতয়ে) দীপ্তি স্থাপন বা হব্য ভক্ষণের জন্য (আ য়াহি) প্রাপ্ত হও। কোথায় তুমি? (গৃণানঃ) স্তুতিকৃত আর (হোতা) হব্য পদার্থকে গ্রহণের জন্য সুষুপ্ত অবস্থা হইতে দৃশ্যমান হও। (ৰর্হিষি) যজ্ঞে (নি সৎসি) বিরাজমান হও (হব্যদাতয়ে) বায়ু আদি দেব যেন হব্যাদির ধোঁয়া যথা স্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারে।। ১।।
এই মন্ত্রে শ্লেষালঙ্কার এবং ‘তয়ে, তয়ে’ এর মধ্যে ছেকানুপ্রাস হইয়াছে।। ১।।
ভাবার্থঃ–যেরূপ বিদ্বান পুরোহিত পবিত্র যজ্ঞাসনে উপবিষ্ট হইয়া যজ্ঞকে সঞ্চালিন করেন, তদ্রুপ রাজা রাজ-সভাতে আসীন হইয়া রাষ্ট্রের উন্নতি করেন। ঐরূপই সমগ্র বিশ^ রচনার অন্তর্যামী গুণবাচক অগ্নি নাম সদৃশ পরমাত্মা আমাদিগের হৃদয় অন্তরিক্ষে প্রকাশিত করেন আমাদিগের জ্ঞানের আলোকবর্তিকা দ্বারা মহান কল্যাণ করেন, এইজন্য সকল মনুষ্যদিগের তাঁহারই শরণ করা উচিত। সকল মনুষ্যদিগের হৃদয়ে পরমাত্মা প্রথম থেকেই সূক্ষ্মাবস্থায় বিরাজমান, তাঁহার পরও মনুষ্য কেন সেই পরমাত্মাকে ভূলিয়া থাকেন? ইহার কারণ পরমমাত্মা তাঁহাদিগের বা অজ্ঞদিগের হৃদয়ে না থাকিবার সমান অর্থাৎ অজ্ঞগণ নিজ হৃদয়ে সেই জ্ঞান-স্বরূপ নিরাকার পরমাত্মাকে জানিতে পারেন না। এইজন্য পরমাত্মাকে পুনঃ আহ্বান করা হইয়াছেন। অভিপ্রায় এরূপ, সকল মনুষ্যদিগের নিজ বুদ্ধিরূপ হৃদয়ে ও৩ম্ এর সত্তা চিন্তন করা এবং পরমাত্মার অর্থাৎ বেদ হইতে সৎ কর্মের প্রেরণা গ্রহণ করা।। ১।।
এখানে বিদ্বানবাচী পৌরহিত্য বিষয় আলোচনা না করিলে নয়, কারণ পৌহিত্যের নামে সমাজে অপৌরহিত্যের কর্ম চলিয়া থাকে আর চলিতেছে (শুধু পৌরাণিক সমাজে নয় আর্য সমাজেও এরূপ কার্য চলিয়া থাকে)। পৌরহিত্য কর্ম শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ বর্ণের অধিকার অন্য বর্ণের নহে! এরূপ শাস্ত্রে ধ্বনিত হইয়াছেÑÑব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতির্বার্হস্পত্যো ব্রাহ্মণো দেবতয়া, স্বামীর দেবতাং পুরোধায়া উপাসরৎ, স্বৈনং দেবতা পুরোধাং গময়তি (মৈ০ স০ ২.২.৩) ব্রহ্মই বৃহস্পতি হয় আর বৃহস্পতি দ্বারাই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হয়। অতঃ পৌরহিত্য প্রাপ্তির জন্য ব্রাহ্মণ স্বকীয় আরাধ্যদেব পিতৃতুল্য বৃহস্পতির নিকট পৌঁছায়। এই উপযুক্ত তথ্য এবং বাক্য দ্বারা স্পষ্ট হয়। বার্হস্পত্যো ব্রাহ্মণো দেবতয়া স্বামীর দেবতাং পুরোধায়া উপাসরৎ অতঃ ইহা দ্বারা সিদ্ধ হয় যে পৌরহিত্য কর্ম ব্রাহ্মণের। অন্য বর্ণের নয়।
সামনে কহিয়াছেন যে যদি কোনও প্রকার পৌরহিত্য পদ প্রাপ্ত না হইবে তো ইন্দ্রাবার্হস্পত্য হবি (মৈ০ স০ ২.২.৪) জ্ঞান প্রাপ্তি করে। অর্থাৎ ব্রহ্ম আর ক্ষত্র উভয় প্রকারের শক্তিকে সংযুক্ত তথা সমন্বিত করিয়া নিজের অন্তর উদ্ভূদ্ধ করেন; ঐরূপ ব্যক্তি যাঁহার মধ্যে ব্রহ্ম-শক্তির সহিত ইন্দ্র-শক্তি অর্থাৎ ক্ষত্র-শক্তিও প্রভূত মাত্রাতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই সকল কর্ম-বিধানে জিজ্ঞাসা করেন। উপদেশ গ্রহণ করেন আর পৌরহিত্য কর্ম করান। পরন্তু এই ইন্দ্রাবার্হস্পত্য-চরু এর জ্ঞান প্রাপ্তি ব্রাহ্মণই করেন, ক্ষত্রিয় নহে। ক্ষত্রিয়ের জন্য তো মনু মহারাজের স্পষ্ট আদেশ—(মনুস্মৃতি ১০.৯৫, ৯৭)।
মন্ত্রে অগ্নি পদ দ্বারা অনেক অর্থ দেখিয়া কিছু সামন্য মানব শঙ্খা করিতে পারেন যে বেদে এরূপ দৃশ্যমান কেন; ইহার কারণ কি? উত্তরঃ-য়াস্কাচার্যের অভিমত বেদের একই মন্ত্রে তিন প্রকারের অর্থ হইয়া থাকেন তথা–
তাস্ত্রিবিধা ঋচঃ। পরোক্ষকৃতাঃ। প্রত্যক্ষকৃতাঃ। আধ্যাত্মিক্যশ্চ। (নিরু০ ৭.১)
অর্থাৎ (তাঃ) সেই (ঋচঃ) ঋচা (ত্রিবিধাঃ) তিন প্রকারের হয়-(পরোক্ষকৃতাঃ) পরোক্ষকৃত=(পরোক্ষরূপে অর্থের প্রকাশকারী), (প্রত্যক্ষকৃতাঃ) প্রত্যক্ষকৃত=[প্রত্যক্ষরূপে অর্থের প্রকাশকারী] (চ) আর (আধ্যাত্মিক্যঃ) আধ্যাত্মিকী [জীবাত্মা, শরীর এবং ও৩ম্ সম্বন্ধী অর্থের প্রকাশকারী]।
অথ প্রত্যক্ষকৃতা মধ্যমপুরুষয়োগাস্ত¡মিতি চৈতেন সর্বনাম্না। (নিরু০ ৭.২)
অর্থাৎ (অথ) আর (প্রত্যক্ষকৃতাঃ) প্রত্যক্ষকৃত ঋচা (মধ্যমপুরুষয়োগাঃ) মধ্যম পুরুষের যোগ (চ) আর (ত্বম্ ইতি) ত্বম্ (এতেন) এই (সর্বনাম্না) সর্বনাম দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকেন।
এইজন্য বেদে অগ্নি আদি পদ দ্বারা প্রত্যক্ষ বিদ্বান আদি দেবতা (ব্যবহারিক) মধ্যম পুরুষের প্রয়োগ এবং (তুমি আপনি) ইহা সর্বনাম দ্বারা সম্বোধন করিয়া বর্ণন করিয়াছেন অর্থাৎ বেদের এই শৈলী (বিশিষ্টার্থক) হইয়া থাকেন। যেখানে প্রত্যক্ষ বিদ্বান-রাজা আদির বর্ণন, এই কৌশল দ্বারা করিয়া থাকেন। এইরূপ সকল বিষয় জানিবেন।
অগ্নিকে অগ্নিকু-ে আহ্বান অর্থাৎ উৎপাদন করা উচিৎ কারণ হোমে প্রদান দ্রব্যকে বায়ু আদিতে বিস্তার আর অর্পণকৃত জ¦লন্ত পদার্থ হইতে উদগত বাতাসে দৃশ্যমান কার্বন বা অন্য কোনও পদার্থের কণা; অদৃশ্য ক্ষতিকারক জীবানু মুক্ত ধূম বা ধোঁয়া প্রদান করিয়া প্রসারিত বা ভক্ষণ করিবার জন্য। প্রশ্নঃ সেই অগ্নি কেমন? উত্তরঃ বিদ্যুৎ অগ্নি, সূর্যাগ্নি ও যজ্ঞাগ্নি যাঁহাদিগের স্তুতি হয় অর্থাৎ শ্রদ্ধা দ্বারা সদোপযোগ উৎপন্ন হয়। প্রশ্নঃ অগ্নি আদি জড় পদার্থের স্তুতি দ্বারা কি কোনও ফল লাভ হইবে? উত্তরঃ যে প্রকার পরমেশ^রের স্তুতি অর্থাৎ গুণানুবাদ করিয়া উহাতে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়; এই প্রকার অগ্নি আদি জড় পদার্থের গুণ বর্ণন করিয়া সেই গুণের দ্বারা উপকার লইবার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইয়া থাকেন অর্থাৎ হোমাদি করিবার ফল লাভ! শিল্পাদিতে অগ্নির কি উপযোগ হয় এইরূপ ইত্যাদি কর্ম বিদিত হইয়া থাকেন। এইজন্য গুণকীর্ত্তন ব্যর্থ নহে।
এই মন্ত্রে অগ্নিই দেবতা অর্থাৎ অগ্নিরই এখানে বর্ণন=স্তুতি। অগ্নি শব্দ মুখ্য হইয়া পরমাত্মার বাচক করিয়া ঈশ^র, বৈজ্ঞানিক, যাজ্ঞিক, ও ব্যবহারিক পক্ষে শ্লেষালঙ্কার যুক্ত অর্থ এই আধার হইয়া থাকেন।
বেদে প্রায়ঃ শ্লেষালঙ্কার দ্বারা অধিক অর্থ প্রতিপাদিত হইয়া আধ্যাত্মিক পরমার্থ বিষয়ক পদের বর্ণন বেদানুকূল ঋষিগণ স্বীকার করিয়াছেন—-
সর্বে বেদা য়ৎপদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ য়দ্বদন্তি। য়দিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য়ং চরন্তি
তত্তে পদংসংগ্রহেণ ব্রবীম্যোম্ ইত্যেতৎ।। (কঠ০ উ০ ২.১৫)
অর্থাৎ (সর্বে বেদাঃ) চার বেদ (য়ৎ) যে (পদম্) পদের (আমনন্তি) বর্ণন করেন, (সর্বাণি) সমস্ত (তপাংসি চ) তপ এবং নিয়মাদি (য়ৎ) যে পদের (বদন্তি) কথন করেন। (য়ৎ) যে পদের (ইচ্ছন্তঃ) ইচ্ছা করিয়া (ব্রহ্মচর্য়্যম্) ব্রহ্মচর্য নিয়মের (চরন্তি) আচরণ করেন; (তৎ) সেই (পদম্) পদকে (তে) তোমার [নচিকেতার] জন্য (সংগ্রহেণ) সংক্ষেপে (ওম্) ও৩ম্ (ইতি) প্রতিপাদন হয় (এতৎ) ইহা (ব্রবীমি) কহিতেছি। এই ওঙ্কারের বিষয় ঋষি পাতঞ্জলি কহিয়াছেনÑÑ
তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।। (যো০ দ০ ১.২৭) অর্থাৎ (তস্য) সেই ঈশ^রের (বাচকঃ) বাচক=বোধক শব্দ=নাম (প্রণবঃ) প্রণব=ও৩ম্। এই সূত্রের ভাষ্য ঋষি ব্যাসদেব করিয়াছেন—-
বাচ্য ঈশ্বরঃ প্রণবস্য। কিমস্য সংকেতকৃতং বাচ্যবাচকত্বমথ প্রদীপপ্রকাশবদব-স্থিতমিতি? স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ। সংকেতস্তীশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি। য়থাঽবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সংকেতেনাবদ্যোত্যতে, অয়মস্য পিতা, অয়মস্য পুত্র ইতি।
সর্গান্তরেষ¦পি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষস্তথৈব সংকেতঃ ক্রিয়তে। সম্প্রতিপত্তিনিত্য-তয়া নিত্যঃ শব্দার্থসম্বন্ধ ইত্যাগমিনঃ প্রতিজানতে।।
অর্থাৎ (প্রণবস্য) প্রণব=ওম্ এর (বাচ্যঃ) বাচ্য (ঈশ^রঃ) ঈশ^র। (প্রশ্ন) (কিম্) কেন (অস্য) ঈশ^র আর প্রণবের (বাচ্যবাচকত্বম্) বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ (সংকেতকৃতম্) সংকেতকৃত অর্থাৎ কৃত্রিম (অথ) অথবা (প্রদীপপ্রকাশবৎ) প্রদীপ আর তাঁহার প্রকাশের সমান (অবস্থিতম্) অবস্থিত=স্থায়ী=নিত্য? (উত্তর) (অস্য বাচ্যস্য) সেই বাচ্য রূপ ঈশ^রের (বাচকেন সহ) বাচক রূপ প্রণবের সহিত (সম্বন্ধঃ) সম্বন্ধ (স্থিতঃ) প্রথম থেকেই স্থিত অর্থাৎ এই সম্বন্ধ স্থায়ী=শাশ^ত। (ঈশ^রস্য) ঈশ^রের (সংকেতঃ) সংকেত (তু) তো (স্থিতম্ এব অর্থম্) প্রথম থেকেই স্থিত সম্বন্ধরই (অভিনয়তি) প্রকাশিত করিয়া থাকে। (য়থা) যে প্রকাশ দ্বারা (পিতাপুত্রয়োঃ) পিতা আর পুত্র (অবস্থিতঃ) প্রথম থেকেই স্থিত=নিয়ত (সম্বন্ধঃ) সম্বন্ধ (সংকেতেন) সংকেতের দ্বারা (অবদ্যোত্যতে) প্রদর্শিত করিয়া যায়=প্রকাশিত করিয়া যায় (অয়ম্) এই (অস্য) ইহার (পিতা) পিতা, (অয়ম্) এই (অস্য) ইহার (পুত্রঃ ইতি) পুত্র।
(সর্গান্তরেষু) অন্য সর্গ-(সৃষ্টি উৎপত্তির)=কল্পে (অপি) ও (বাচ্যবাচক-শক্ত্যপেক্ষঃ) বাচ্য-বাচক শক্তির অপেক্ষা দ্বারা (তথৈব) সেই প্রকারের (সংকেতঃ) সংকেত (ক্রিয়তে) করিয়া যায়। (সম্প্রতিপত্তিনিত্যতয়া) সদৃশ্য ব্যবহারের পরম্পরার প্রবাহ রূপে নিত্য হওয়াই (শব্দার্থসম্বন্ধঃ) শব্দ তথা অর্থ রূপী বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ (নিত্যঃ ইতি) নিত্য, এই (আগমিনঃ) বেদ মান্যকারী নতুন শাস্ত্রকার
(প্রতিজানতে) কহিয়া থাকেন, মান্য করেন।
মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অর্থ করিয়াছেন—-(তস্য বা০) ঈশ^রের যে ওঙ্কার নাম, তাঁহা পিতা-পুত্রের সম্বান্ধের সমান আর এই নাম ঈশ^র ব্যতীত দ্বিতীয় অর্থ (অগ্নি আদি) বাচী হয় না। ঈশ^রের যত নাম রহিয়াছেন, উহার মধ্য হইতে ওঙ্কার সব চাইতে উত্তম নাম। (ঋ০ ভা০ ভূ০ উপাসনাবিষয়)।
(ও৩ম্) এই ওঙ্কার শব্দ পরমেশ^রের সর্বোত্তম নাম। কেননা ইহার মধ্যে অ, উ আর ম্ তিন অক্ষর মিশ্রিত এক (ও৩ম্) সমুদায় নির্মাণ। এই এক নাম দ্বারা পরমেশ^রের অনেক নাম আসিয়া যায়। যেরূপÑঅকার দ্বারা বিরাট অগ্নি আর বিশ্বাদি। উকার দ্বারা হিরণ্যগর্ভ, বায়ু, তৈজসাদি। মকার দ্বারা ঈশ্বর, আদিত্য আর প্রজ্ঞাদি নামের বাচক এবং গ্রাহক। (স০ প্র০ প্রথম সমু০)।
সব বেদাদি শাস্ত্রে পরমেশ^রের প্রধান আর নিজ নাম (ও৩ম্) কহিয়াছেন, অন্য সব গৌণিক নাম। (স০ প্র০ প্রথম সমু০)।
ওঙ্কারের বাচ্য ঈশ্বর আর উহার বাচক ওঙ্কার। বাহ্য বিষয়ে ইহাই গ্রহণ করা উচিত অন্য কিছু নয়। (পশ্চি০ বা০ হুগলী শাস্ত্রার্থ)।
যখন অগ্নি আদি পদ দ্বারাও যদি পরমাত্মা ও বিভিন্ন অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন তাঁহা যুক্তিযুক্ত হইয়া থাকেন, চারবেদ পরমাত্মা ও সৃষ্টি বিদ্যার বর্ণন করিয়া থাকেন। বাস্তবে যে প্রকাশ আদি গুণ রহিয়াছেন, তাঁহা পরমাত্মাতে অসীম (সীমাহীন) ভাব দ্বারা বর্তমান। এইজন্য অগ্নি আদি পদের মুখ্য অর্থ পরমাত্মা, পরন্তু পরমাত্মার প্রকাশ আদি গুণ সসীম (সীমাযুক্ত) হইয়া অগ্নি আদি ভৌতিক
পদার্থেও কিছু অংশ পর্যন্ত বিস্তার থাকেন। সেই অংশ ভৌতিক পদার্থকে দেবতা কহিয়াছেন।
এইজন্য সম্পূর্ণ দেবতা বাচক পদে পূর্ণভাব সেই পরমাত্মাই বেদে প্রকাশিত, যেরূপ যৌগিক অর্থে ভৌতিক পদার্থেও প্রকাশিত হয় জানা উচিত। এই প্রকার কাত্যায়নের গুরু আচার্য শৌনকের অভিমত বেদের সর্বত্র প্রকরণ—-
ঋষিম্ তু প্রথমম্ ব্রƒয়াচ্ছন্দস্তু তদনন্তরম্। দেবতামথ মন্ত্রাণাম্ কর্মস্বেবমিতি
শ্রুতিঃ।। (বৃহদ্দেবতা০ ৮.১৩৮)
অর্থাৎ মন্ত্রার্থকে জানিবার জন্য সর্বপ্রথম সেই মন্ত্রের ঋষিকে জানা উচিত, উহার পশ্চাৎ ছন্দ এবং দেবতাকে জানিয়া সেই মন্ত্রকে কর্মে বিনিয়োগ করা উচিত অর্থাৎ কর্মের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক আদি অর্থকে জানা উচিত। এইজন্য য়াস্কাচার্য অভিমত—
অয়ং মন্ত্রার্থচিন্তাভ্যূহোঽভ্যূঢ়োঽপি শ্রুতিতোঽপি তর্কতো নতু পৃথক্তে¦ন মন্ত্রা নির্বক্তব্যাঃ, প্রকরণশ এব তু নির্বক্তব্যাঃ। ন হ্যেষু প্রত্যক্ষমস্ত্যমৃষেরতপসোবা, পারোবর্য়্যবিৎসু তু খলু বেদিতৃষু মৃয়োবিদ্যঃ প্রশস্যো ভবর্তাত্যুক্তং পুরস্তাৎ, মনুষ্যা বা ঋষিষূৎক্রামৎসু দেবানব্রুবন্, কো ন ঋষির্ভবিষ্যতীতি তেভ্য এতং তর্কমৃষিং প্রায়চ্ছন্ মন্ত্রার্থচিন্তাভ্যূঢ় হং তস্মাদ্ য়দেবং কিঞ্চানূচানোঽভ্যূহত্যার্ষং তদ্ভবতি। (নিরু০ ১৩.১২)
অর্থাৎ (ইতি অয়ম্) এই প্রকার (মন্ত্রার্থচিন্তাঽভ্যূহঃ) মন্ত্রার্থ চিন্তন বিষয়ক (অভ্যূঢ়ঃ) প্রাপ্ত করিয়া থাকেন। (অপি শ্রুতিতঃ অপি তর্কতঃ) মন্ত্রার্থ চিন্তন শ্রুতির অনুসার আর তর্কের অনুসার হওয়া উচিত। (ন তু পৃথক্তে¦ন মন্ত্রা নির্বক্তব্যাঃ) আর প্রকরণ হইতে পৃথক করিয়া মন্ত্রের নির্বচন করা উচিত নয়Ñ(প্রকরণশ এব তু নির্বক্তব্যাঃ) কিন্তু প্রকরণ অনুসারেই নির্বচন করা উচিত। (নহি এষু প্রত্যক্ষম্ অস্তি অনৃষেঃ অতপসঃ বা) আর এই মন্ত্রের অর্থের প্রতীতি সেই সামান্য ব্যক্তির হয় না, যিনি ঋষি অর্থাৎ মন্ত্রার্থ দ্রষ্টা নয় অথবা যিনি তপের সাধনা করেন না (পুরস্তাৎ)Ñপ্রথমে (ইতি উক্তম্) এই বচন কহিয়াছি যে (পারোবর্য়বিৎসু বেদিতৃষু) বেদজ্ঞ বিদ্বানের মধ্যে (ভূয়োবিদ্যঃ) অধিক [সূক্ষ্ম আর্ষ দৃষ্টির] বিদ্যাবান মনুষ্য (প্রশস্যঃ ভবতি) প্রশংসনীয় কথন করেন।
আর উপনিষদে ধ্যানোপাসনা অথবা বেদের অর্থ-প্রত্যক্ষ করিবার বিধি দিয়া লিখিয়াছেন—-
য়স্যামৃচি তামৃচং য়দার্ষে য়ং তমৃষিং য়াং।
দেবতামভিষ্টোষ্যন্ স্যাৎ তাং দেবতামুপধাবেৎ।। (ছান্দগ্য০ উ০ ১.৩.৯)
অর্থাৎ যে (য়স্যাম্ ঋচি) ঋচাতে পরমাত্মার বর্ণন (তাম্ ঋচম্) সেই ঋচার (উপধাবেৎ) বিচার করিবেন; (য়ৎ) যে (আর্ষেয়ম্) সেই ঋচার ঋষি (তম্ ঋষিম্) সেই ঋষির (উপধাবেৎ) বিচার অর্থাৎ উহার গুণ, কর্ম স্বভাব সম্বন্ধী ইতিহাসের চিন্তন করিবেন। (য়াম্) যে (দেবতাম্) মন্ত্রস্থ দেবতা=মন্ত্রার্থ বিষয়ে (অভিস্তোষ্যন্) স্তুতি (স্যাৎ) হউক (তাম্ দেবতাম্) সেই দেবতা [বিষয়ক] (উপধাবেৎ) চিন্তন করিবেন।
এইজন্য য়াস্কাচার্যও অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন—-
সাক্ষাৎকৃতধর্মাণ ঋষয়ো ৰভূবুঃ। তেঽবরেভ্যোঽসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্য উপদেশেন মন্ত্রান্ সম্প্রাদুঃ। উপদেশায় গ্লায়ন্তোঽবরে ৰিল্মগ্রহণায়েমং গ্রন্থং সমা¤œাসিষুঃ। বেদং চ বেদাঙ্গানি চ। ৰিল্মং ভিল্মং ভাসনমিতি বা। (নিরু০ ১.২০)
অর্থাৎ প্রারম্ভে (সাক্ষাৎকৃতধর্মাণঃ) ধর্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করিয়া (ঋষয়ঃ) ঋষি (ৰভূবুঃ) হইয়াছেন, (তে) তাঁহারাই (অবরেভ্যঃ) পরবর্তী (অসাক্ষাৎকৃতধর্মভ্যঃ) ধর্মের সাক্ষাৎকার রহিত মানবের জন্য (উপদেশেন) উপদেশের মাধ্যমে (মন্ত্রান্) মন্ত্রকে (সম্প্রাদুঃ) প্রদান করিয়াছেন। (উপদেশায়) উপদেশ গ্রহণ করিতে (গ্লায়ন্তঃ) অসমর্থ (অবরে) পরবর্তী জন্মের জন্য (ৰিল্মগ্রহণায়) স্পষ্টতা পূর্বক জানাইবার জন্য (ইমম্) এই (গ্রন্থম্) নিঘণ্টু কোষের (সমা¤œাসিষুঃ) সমা¤œান করিয়াছেন (চ) আর (বেদম্) বেদ তথা (বেদাঙ্গানি চ) বেদাঙ্গ। (ৰিল্মম্ ভিল্মম্ ভাসনমিতি বা) ‘ৰিল্ম’ এর অর্থ ‘ভিল্ম’ যাঁহা প্রকাশ করা।
আধিদৈবিক; আধিভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক ইহার মধ্যে চার বেদে আধিদৈবিক অর্থ মূখ্য=বিজ্ঞান পরক জানা উচিত।
ঐরূপ সিদ্ধ হইবার পর যদি সব বিদ্যার আকারভূত বেদকে বৈদিক-ধর্মানুযায়ী প্রাণ হইতেও প্রিয় মান্য করেন, তাঁহা হইলে ইহাতে আশ্চার্যের কি?
মন্ত্রের অনেক অর্থ স্বচ্ছন্দ (সহজ) হয় না, কিন্তু ব্যবস্থিত হয়; আর সেই ব্যবস্থা প্রাচীন মহর্ষিগণ ত্রিবিধ প্রক্রিয়া রূপে স্থাপিত করিয়াছেন। উহাদিগের অনুসার এক অর্থ যাজ্ঞিক, দ্বিতীয় আধিদৈবিক এবং তৃতীয় আধ্যাত্মিক হইয়া থাকেন। কিন্তু মুনি জৈমীনির উপদেশ….সতঃ পরমবিজ্ঞানম্।। ( মীমা০ সূ০ ১.২.৪৯)
অর্থাৎ অবিজ্ঞানম্ যে মন্ত্রের অর্থে অবিজ্ঞান কথিত আছে, তাঁহা অজ্ঞানতা বশতঃ সতঃ পরম্ কেবল বিদ্যমান অর্থকেই জানা উচিত নয়।
প্রাচীন কালে বৈদিক বিদ্বানগণ বেদের পূর্ব-নির্দিষ্ট ত্রিবিধ অর্থ করিতেন এই বিষয়ে কিছু প্রমাণ—-
১.ভগবান য়াস্ক-বাচং শুশ্রবাঁ অফলামপুষ্পাম্ ঋ০ ১০.৭১.৫ এই ঋগ্বেদ অংশের ব্যাখ্যা করিয়া কহিয়াছেন—-
অর্থং বাচঃ পুষ্পফলমাহয় জ্ঞদৈদতে পুষ্পফলে দেবতাধ্যাত্মে বা। (নিরু০ ১.১৯)
অর্থাৎ (অথম্) অর্থের (বাচঃ) বাণীকে (পুষ্পফলম্) পুষ্প আর ফল (আহ) কহিয়া থাকেন। (পুষ্পফলে) বাণীকে পুষ্প আর ফল ক্রমশঃ (য়াজ্ঞদৈবতে) যজ্ঞ আর দেবতা জ্ঞান হয় অর্থাৎ যজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞান পুষ্প আর দেবতা বিষয়ক জ্ঞান উহার ফল হয়। (বা) অথবা (দেবতাধ্যাত্মে) দেবতা বিষয়ক জ্ঞান পুষ্প আর অধ্যাত্ম (আত্ম বিষয়ক জ্ঞান) উহার ফল।
এই মুনি য়াস্কীয় বচন দ্বারা দানযোগ্য বাণী বেদের যাজ্ঞিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ অর্থ হইয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট জাানা যায়।
২.ভগবান য়াস্ক মুনিরই কেবল প্রতিজ্ঞাই নয়, পরন্তু তিনি নিরুক্তে বর্ণিত সব মন্ত্রের আধিদৈবিক ব্যাখ্যা করিয়াছেনÑসব মন্ত্রের আধিদৈবিক অর্থই প্রধানভূত হয় এরূপ স্পষ্ট প্রতিপাদন করিয়াছেন।
বেদের বাণী আকাশীয়, বেদের দেব আকাশীয়, মন্ত্রগত ঋষি আকাশীয়, ছন্দ আকাশীয়, স্বর আকাশীয় অতঃ বেদে পার্থিব মনুষ্য আর ঋষিদিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব নহে। বেদকে যথার্থ জানিবার জন্য ব্রাহ্মণগ্রন্থ তথা নিরুক্তে বর্ণিত অধিদৈবত আর অধি-যজ্ঞ পরক অর্থের জ্ঞান আবশ্যক।
যে ভাষ্যকার বেদের অধিদৈবত অর্থকে যথার্থ জানিতে পারেননি, তাঁহারাই বেদার্থ নষ্ট করিয়াছেন। বেদের অধ্যাত্ম পরক অর্থ বেদের অধিদৈবত অর্থকে জানা ব্যতীত কদাপি প্রকাশ করা সম্ভব নহে।
য়াস্কাচার্য় অনেক স্থানে আধ্যাত্মিক অর্থ আর যাজ্ঞিক অর্থেরও নির্দেশ করিয়াছেন। যেরূপ—-
(ক) একয়া প্রতিধা পিবৎ সাকং সরাংসি-কাণুকা (ঋ০ ৮৭৭.৪) এই ঋচার ব্যাখ্যা করিতে গিয়া য়াস্ক কহিয়াছেন—-
তত্রৈতদ্ য়াজ্ঞিকা বেদয়ন্তেত্রিংশদুক্থপাত্রাণি মাধ্যন্দিনে সবনে একদেবতানি। তান্যেতস্মিন্ কালে একেন প্রতিধানেন পিবন্তি। তান্যত্র সরাংস্যুচ্যন্তে। ত্রিংদপরপক্ষস্যাহোরাত্রাঃ, ত্রিংশৎপূর্বপক্ষত্যেতি নৈরুক্তাঃ। তদ্ য়া এতাশ্চান্দ্রমস্য আগামিন্য আপো ভবন্তি রশ্ময়স্তা অপরপক্ষে পিবন্তি। (নিরু০ ৫.১১)
অর্থাৎ যাজ্ঞিক মতে মন্ত্র-নির্দিষ্ট তিন সর তিন উক্তসঙ্গক সোম গ্রহ (=পাত্র বিশেষ) হয় আর নৈরুক্তের মতে ৩০ পূর্ব পক্ষ তথা ৩০ অপর পক্ষে অহোরাত্র হয়।
(খ) গৌরমীমেদনু (ঋ০ ১.১৬৪.২৮) আর উপহ্বয়ে সুদুঘাং ধেনুমেতাম্ (ঋ০ ১.১৬৪.২৬) এই ঋচার ব্যাখ্যাতে নিরুক্তকার কহিয়াছেন—-
বাগেষা (গৌঃ ধেনুঃ) মাধ্যমিকা, ধর্মধুগিতি য়াজ্ঞিকাঃ। (নিরু০ ১১.৪২)
অর্থাৎ এই (গৌ ধেনু) মাধ্যমিক বাক্ গৌ হয়। যাজ্ঞিক মতে যজ্ঞার্থ দোহনের গাভী।
(গ) য়ত্রা সুপর্ণাঃ (ঋ০ ১.১৬৪.২১) মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে য়াস্কমুনি কহিয়াছেন—-
য়ত্র সৃপর্ণা সুপতনা আদিত্যরশ্ময়ঃ……………………………………..ইত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম্য়ত্র সুপর্ণাঃ সুপতনানীন্দ্রিয়াণি ইত্যাত্মগতিমাচষ্টে। (নিরু০ ৩.১২)
অর্থাৎ অধিদৈব পক্ষে সুপর্ণা আদিত্যের রশ্মি আর অধ্যাত্মে সুপর্ণা ইন্দ্রিয়।
(ঘ) সপ্তঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে (যজু০ ৩৪.৫৫) এই মন্ত্রের ব্যাখ্যাতে য়াস্ক কহিয়াছেন—-
সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে, রশ্ময়ঃ আদিত্যে ইত্যধিদৈবতম্। অথাধ্যাত্মম্সপ্ত ঋষয়ঃ প্রতিহিতাঃ শরীরে, ষড়িন্দ্রিয়াণি বিদ্যা সপ্তম্যাত্মনি ইত্যাত্মগতিমাচষ্টে। (নিরু০ ১২.৩৭)
অর্থাৎ অধিদৈবতে সপ্ত ঋষি সপ্ত সূর্যরশ্মি আর অধ্যাত্মে ৬ ইন্দ্রিয় (=৫ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন) এবং ৭ বিদ্যা।
এই প্রকার অন্যত্রও অধিদৈবতের সহিত য়াজ্ঞিক তথা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও ভগবান য়াস্ক প্রদর্শিত করিয়াছেন। নিরুক্ত ১৩ হইতে ১৪ অধ্যায়ের প্রায় সমস্ত মন্ত্রের আধিদৈবিক আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান প্রাপ্ত হয়। এইরূপ য়াস্কাচার্যের মতে মন্ত্রের তিন প্রকারের অর্থ প্রামাণিত হইয়া থাকে, ইহা স্পষ্ট জানা যায়।
১.পূর্বনির্দিষ্ট য়াস্কের মতকেই নিরুক্ত টীকাকার শ্রী স্কন্দস্বামী (=মহেশ^র) বিস্তার প্রতিপাদন করিয়া উপসংহার করিতে গিয়া কহিয়াছেন—-
সর্বদর্শনেষু (পূর্বনির্দিষ্টেষু য়াজ্ঞিকাধিদৈবতাধ্যাত্মিকেষু) চ সর্বে মন্ত্রা য়োজনীয়াঃ। কুতঃ? স্বয়মেব ভাষ্যকারেণ সর্বমন্ত্রাণাং ত্রিপ্রকারস্য বিষয়স্য প্রদর্শনা অর্থ বাচঃ পুষ্পফলমাহ ইতি জ্ঞাদীনাং পুষ্পফলত্বেন প্রতিজ্ঞানাৎ। (নিরুক্তটীকা ৭.৫)
অর্থাৎ সব পক্ষ (যাজ্ঞিক, অধিদৈবত আর আধ্যাত্মিক) সব মন্ত্রের যোজনা করা উচিত। কেননা স্বয়ং ভাষ্যকার (=নিরুক্তকার য়াস্ক) সব মন্ত্রের তিন প্রকারের বিষয় দর্শাইয়া অর্থকে মন্ত্ররূপী বাককে পুষ্পফল কহিয়াছেন এবং যজ্ঞ আদিকে পুষ্প বা ফল মান্য করিয়াছেন।
২.নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্যও মন্ত্রের তিন প্রকারের অর্থ হয়, ইহা স্পষ্ট কহিয়াছেন। যেরূপ—-
ক.আধ্যাত্মিকাধিদৈবতাধিয়জ্ঞাভিবায়িনাং মন্ত্রাণামর্থাঃ পরিজ্ঞায়ন্তে।। (নিরুক্তটীকা ১.১৮) অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অধিদৈবত আর অধিযজ্ঞ এই তিন বিষয়ে কথিত মন্ত্রের অর্থ বিদিত হয়।
খ. তত্র-তত্র এক এব হ্যসৌ আদিত্যম-লে আধিদৈবতে চাধ্যাত্মে চ বুদ্ধ্যগি দেবতাভূতঃ, স এব তত্রতত্রোপেক্ষিতব্যঃ।……………অধ্যাত্মেঽপি হৃদয়াকাশাদ্ য়ানীন্দ্রিয়ানি প্রসর্পন্তি ত এব রশ্ময়ঃ, অধিতৈবতে চ ত এব বিশে^দেবা ইত্যুক্তম্্ এবং তত্র-তত্র য়োজ্যম্। প্রকারমাত্রমেবেদমুপপ্রদর্শিতং ভাষ্যকারেণ। (নিরুক্তটীকা ৩.১২) অর্থাৎ [যেখানে-যেখানে বিষ্ণুর কথন] সেখানে-সেখানে অধিদৈবতে আদিত্য ম-ল আর অধ্যাত্মে বুদ্ধির দেবতা রূপ আত্মাকেই জানা উচিত। অধিদৈবতে আদিত্য রশ্মিই বিশে^দেবা আর অধ্যাত্মে হৃদয়াকাশে যে ইন্দ্রিয় প্রকাশিত সেই রশ্মি। এই প্রকার মন্ত্রের যোজনা করা উচিত। ভাষ্যকারই এই প্রকার নির্দেশ করিয়াছেন মাত্র।
গ. তস্মাদেতেষু য়াবন্তোঽর্থা উপপদ্যেরন্ আধিদৈবিকর্ব তে য়োজ্যাঃ, নাত্রাপরাধোঽস্তি। (নিরুক্তটীকা ২.৮) অর্থাৎ আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক আর অধিযজ্ঞে আশ্রিত যত অর্থ উৎপন্ন হয়, সেই সব যোজনা করা উচিত। ঐরূপ করা কোনও অপরাধ নহে। এই প্রকার অন্যেত্রও দুর্গাচার্য মন্ত্রের ত্রিবিধ প্রক্রিয়া দর্শাইয়াছেনÑÑ
৫.বেদজ্ঞে অলঙ্কারভূত, শব্দ-শাস্ত্রের প্রমাণভূত আচার্য ভর্তৃহরিও মন্ত্রের ত্রিবিধ প্রক্রিয়াগম্য অর্থকে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন—-
য়তা ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে (ঋ০ ১.২২.১৭) ইত্যত্র এক এব বিষ্ণুশব্দোঽনেকশক্তিঃ সন্ অধিদৈবতমধ্যাত্মমধিয়জ্ঞং চাত্মনি নারায়ণে চষালে চ তয়া শক্ত্যা প্রবর্ততে। (মহাভাষ্যদীপিকা হ০ লে০, পৃ০ ২৬৮)
অর্থাৎ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে (ঋ০ ১.২২.১৭) মন্ত্রে এক বিষ্ণু শব্দই অনেক শক্তিশালী হইবার কারণ অধিদৈবত, অধ্যাত্ম আর অধিযজ্ঞে ক্রমশঃ আত্মা (সূর্য) নারায়ণ আর চষালে স্বশক্তি দ্বারা প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।
এই প্রকার অন্য আচার্যের মতও এই বিষয়ে প্রকাশিত করিয়াছেন। কিন্তু বিস্তারের কারণে সমাপ্তি করিব। মন্ত্রের বহুবিধ অর্থও পূর্বাযার্চগণই দর্শায়াইছেন।
যথা—-চত্বারি বাক্পরিমিতা পদানি (ঋ০ ১.১৬৪.৪৫) এই ঋচার ছয় প্রকারের অর্থ য়াস্ক মুনি দর্শাইয়াছেন—-
কতমানি তানি চত্বারি পদানি? ওঙ্কারো মহাব্যাহৃতয়শ্চেত্যার্ষম্। নামাখ্যাতে চোপসর্গনিপাতাশ্চেতি বৈয়াকরণাঃ। মন্ত্রঃ কল্পো ব্রাহ্মণং চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি য়াজ্ঞিকাঃ। ঋচো য়জূংষি সামানি চতুর্থী ব্যাবহারিকীতি নৈরুক্তাঃ। সর্পাণাং বাগ্ বয়সাং ক্ষুদ্রস্য সরীসৃপস্য চতুর্থী ব্যাবহারিকীত্যেকে। পষুশু তূনবেষু মৃগেষ্যাত্মনি চেত্যাত্মপ্রবাদঃ।। (নিরু০১৩.৯) অর্থাৎ চার প্রকারের বাক্Ñ(১) ওঙ্কার আর তিন মহাব্যাহৃতি, এরূপ ঋষি মত। (২) নাম-আখ্যান-উপসর্গ-নিপাত, ইহা বৈয়াকরণগণ মান্য করেন। (৩) মন্ত্র, কল্প, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ, ব্যাবহারিকী ভাষা, ইহা যাজ্ঞিকগণ মান্য করেন। (৪) ঋগে¦দ, যজুর্বেদ, সামবেদ আর ব্যাবহারিকী ভাষা, ইহা নৈরুক্তের মত। (৫) সর্প, পক্ষি, ক্ষুদ্র জন্তু সরীসৃপদিগকে আর ব্যাবহারিকী, ইহা আচার্যগণ মান্য করেন। (৬) পশু, বাদ্যযন্ত্র, মৃগদিগকে আর আত্মার এই অধ্যাত্মবাদিগণের কথন।
এইসব কথন যথার্থ প্রকার সমীক্ষা করিয়া নিরুক্তের ব্যাখ্যাকার দুর্গাচার্য কহিয়াছেন—-
(ক) অনুপক্ষীয়মাণশক্তয়ো হি বেদশব্দা য়থাপ্রজ্ঞং পুরুষাণাভর্থাভিধানেষু বিপরিণমমানাঃ সর্বতোমুখা অনেকার্থান্ প্রব্রুবন্তীতি। (নিরুক্তটীকা ১.২০)
অর্থাৎ বৈদিক শব্দের অভিধান-শক্তিবান, ক্ষীণশীল নহে। পুরুষের প্রজ্ঞা শক্তি যেরূপ হয়, তদ্রুপ বৈদিক শব্দ অর্থে পরিণত হইয়া থাকেন। তাঁহা সর্বদিকে মুখ স্বরূপ অনেকবিধ অর্থকে কহিয়া থাকেন।
(খ) নহ্যেতেষু অর্থস্যেয়ত্তাবধারণমস্তি। মহার্থা হ্যেতে দৃস্পরিজ্ঞানাশ্চ। য়থাশ্বারোহবৈশিষ্ট্যাদশ্বঃ সাধুঃ সাধুতরশ্চ বহতি, এবমেত বক্তৃবৈশিষ্ট্যাৎ সাধূন সাধুতরাংশ্চার্থান্ব্রন্তি।। (নিরুক্তটীকা ২.৮)
অর্থাৎ অন্ত্রে অর্থের সীমা হয় না। ইহার মাহার্থ (=অনেক অর্থদ্বারা) যুক্ত হয় আর কঠিনতা দ্বারা প্রকাশিত হয়। যেরূপ অশে^র উপর উপবিষ্টকারীর বিশেষতার অনুসার অশ^ তেজ আর তেজস্বী হইয়া থাকেন, তদ্রুপ অর্থকারীর প্রজ্ঞা শক্তির অনুসার মন্ত্র সাধক আর সাধুতর অর্থকে প্রকট করেন।
এই পূর্বাচার্যদিগের প্রমাণ দ্বারা ইহা সর্বদা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, বেদ কেবল দ্রব্যময় যজ্ঞের জন্যই প্রবৃত্ত হয়নি। তাঁহা সর্ববিদ্যার আর সর্ববিধ জ্ঞানের ভার। সেখানে যে আধিদৈবিক অর্থ হয়, তাঁহা সাক্ষাৎ বিজ্ঞানপরক আর তাঁহাও অনেকবিধ হইয়া থাকেন। উহার নির্দেশ পরে করিব। আধ্যাত্মিক অর্থও আত্মা-শরীর-পরমাত্মা সম্বন্ধ দ্বারা তিন প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকেন।
শেষ যে যাজ্ঞিক অর্থ হয়, তাঁহাও উত্তম মহত্ত্বের হইয়া থাকেন। পরন্তু যেরূপ আজকালের যাজ্ঞিক মনুষ্য যজ্ঞের ব্যাখ্যা করেন, সেই প্রকার এই তর্ক প্রধান যুগে সেই অর্থ উহার মহত্ত্বকে প্রতিপাদন করিতে পারেন না। বস্তুতঃ ইহার কারণ যজ্ঞ প্রক্রিয়ার মূলে পরিজ্ঞানের অভাবই থাকিয়া যায়। এইজন্য এখানে নিদর্শন মাত্র নিত্যরূপ দ্বারা বিহিত শ্রৌতযজ্ঞের বাস্তবিক প্রয়োজন জানানো উচিত—-
বৈদিক সাহিত্যের অনেকবার পরিশীলন দ্বারা আমি ইহা জানিয়াছি যে নিত্যরূপ দ্বারা বিহিত অগ্নাধান হইতে লইয়া সহস্র সংবৎসর পর্যন্ত সাধ্য (=শীল) যেমন শ্রৌতযজ্ঞ রহিয়াছেন, তাঁহা এই ব্রহ্মা-ে স্বর্গ হইতে লইয়া প্রলয় পর্যন্ত যে অতীন্দ্রিয় যজ্ঞ নিস্পন্ন হইয়াছেন বা হইতেছেন, উহার স্বরূপের জ্ঞাপন প্রদানের জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই বিরাট পুরুষ=ব্রহ্মা-ে দেব=প্রাকৃতিক তত্ত্বের দ্বারা যে যজ্ঞ করিয়াছেন বা করিতেছেন, উহারই আধার পুরুষ সূক্তের এই মন্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছেন—-
য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাস্তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত
য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ।। (ঋ০ ১০.৯০.১৬) এই আধিদৈবিক যজ্ঞ প্রতিপাদক মন্ত্রের ব্যাখ্যা ভগবান য়াস্ক মুনিই এই প্রকার করিয়াছেন—-
য়জ্ঞেন য়জ্ঞময়জন্ত দেবাঃ, অগ্নিনাঽগ্নিময়জন্ত দেবাঃ। অগ্নিঃ পশুরাসীৎ তমালভন্ত তেনাজয়ন্ত ইতি চ ব্রাহ্মণম্। তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্। তে হ নাকং মহিমানঃ সংবসেব্যন্ত। য়ত্র পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ সাধনাঃ। দ্যুস্থানো দেবগণ ইতি নৈরুক্তাঃ! (নিরু০ ১২.৪১)
অর্থাৎ দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করেন, দেবগণই অগ্নি দ্বারা অগ্নির যজন করেন। অগ্নি পশু, উহার আলম্ভন করেন, উহা হইতে যজনা করেন, ইহা ব্রাহ্মণের কথন। সেই যজ্ঞই প্রধান কর্ম ছিল। উহা হইতে দেবগণই স্বর্গ প্রাপ্ত হইতেন। যেখানে পূর্বকালিক যজ্ঞ প্রদানকারী দেব ছিলেন। এই দেব দ্যুস্থানীয় দেবগণ, ঐরূপ নৈরুক্তকারের মত।
যেরূপ বর্তমানকালে ভূগোল-খগোল শাস্ত্র জ্ঞানের জন্য যেরূপ অনেক প্রকারের চিত্র নির্মাণ করিয়া যান অথবা অতীন্দ্রিয় প্রাচীন ঘটনা বা বাক্যের বোধ প্রদানের জন্য রঙ্গমঞ্চে নাটক প্রদর্শন করেন, তদ্রুপই ব্রহ্মা-ের বিজ্ঞানকে প্রাপ্ত প্রদানের জন্য বিবিধ শ্রৌত যজ্ঞের বিধান প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইজন্য শ্রৌত যজ্ঞের বিধানকে যথাবৎ জানিয়া তাঁহার প্রকৃতিভূত ব্রহ্মা-ের বিজ্ঞান উত্তম প্রকার জানিয়া থাকেন।
এই পরমোপযোগী শ্রৌত যজ্ঞতত্বকে স্পষ্ট করাইবার জন্য যাজ্ঞিক বলাধান-কর্মের ক্রিয়ার নির্মাণ বৈদিক গ্রন্থের উদাহরণ দ্বারাই সেই বলাধান কর্মের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন—-
যখন শ্রৌত যজ্ঞকে সৃষ্টি বিজ্ঞানেরই পৃষ্ঠভূমি হয়, তখন যাজ্ঞিক-প্রক্রিয়ার দ্বারা কৃত অর্থও সৃষ্টি বিজ্ঞানের প্রতিপাদকই হইয়া থাকেন। এইজন্য বেদের বৈজ্ঞানিক অর্থই মুখ্যার্থ হইয়া থাকেন। [য়ৎপি-ে তদ্ ব্রহ্ম-ে] (=যাঁহা পি-ে থাকেন, তাঁহাই ব্রহ্মাণ্ডে) বচনানুসার সৃষ্টি-বিজ্ঞানেরও অধ্যাত্মেই পরিণতি হইয়া থাকেন। এইজন্য এই শ্রুতি প্রবৃত্ত হইয়াছেন—-
য়স্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি (ঋ০ ১.১৬৪.৩০)। বেদের যাজ্ঞিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক অর্থ অধিক সূক্ষ্ম। উহাতে সকলের বুদ্ধি প্রবেশ করিতে পারেন না।
পরন্তু বেদের ব্যাবহারিক অর্থ দ্বারা সাধারণ মনুষ্যও বৈদিক শিক্ষার অনুকূল নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ আর সুখী তৈরী করিতে পারেন। ইহাকে ঋষিদেব দয়ানন্দ সরস্বতী প্রাচীন ঋষিদিগের মনের বিচার স্বীকৃত মার্গের আশ্রয় লইয়া মন্ত্রের ব্যাবহারিক অর্থ প্রধানতা দিয়াছেন। তাঁহার নিজের ঋগে¦দাদিভাষ্য ভূমিকার প্রতিজ্ঞা বিষয়ে কহিয়াছেন—-
অথাঽত্র য়স্য য়স্য মন্ত্রস্য পারমার্থিকব্যাবহারিকয়োর্দ্বয়োরর্থয়োঃ শ্লেষালঙ্কারাদিনা সপ্রমাণঃ সম্ভবোঽস্তি, তস্য দ্বৌ দ্বাবথৌ বিদাস্যেতে। য়ত্র খলু ব্যাবহারিকার্থো ভবতি…। (ঋ০ ভা০ ভূ০ পৃষ্ঠ০ ৩৬২) অর্থাৎ যেখানে-যেখানে মন্ত্রের পারমার্থিক আর ব্যাবহারিক দুই অর্থকে শ্লেষাদি অলঙ্কার দ্বারা স্ব-প্রমাণ সম্ভব হইয়া থাকেন, সেখানে-সেখানে মন্ত্রের দুই-দুই অর্থ লিখিবেন।…….যাঁহা নিশ্চয়ই কেবল ব্যাবহারিক অর্থ……।
যাজ্ঞিক, আধিদৈবক, আধ্যাত্মিক অর্থ প্রাচীন মহর্ষিগণ নিজ-নিজ গ্রন্থে যেখানে-সেখানে প্রদর্শিত করিয়াছেন। এইজন্য সেই প্রকারের অর্থ মহর্ষি স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী করেননি। ইহাও তিনি কহিয়াছেন—-
পরন্তে¡তৈর্বেদমন্ত্রৈঃ কর্মকা-বিনিয়োজিতৈর্য়ত্র য়ত্রাগ্নিহোত্রাদ্যশ^মেধান্তে য়দ্যৎকর্তব্য তত্তদত্র বিস্তরশো ন বর্ণয়িষ্যতে। কুতঃ? কর্মকা-ানুষ্ঠানস্যৈতরেয়শতপথব্রাহ্মণ পূর্বমীমাংসা-শ্রৌতসূত্রাদিষু য়থার্থ বিনিয়োজিতত্বাৎ। পুনস্তৎকথনেনানৃষিগ্রন্থবৎ পুনরুক্তিপিষ্টপেষণদোসাপত্তেশ্চেতি। (ঋ০ ভা০ ভূ০ পৃষ্ঠ০ ৩৬২)
অর্থাৎ কর্মকাণ্ডে বিনিয়োগযুক্ত এই বেদ মন্ত্র দ্বারা অগ্নিহোত্র হইতে লইয়া অশ^মেধ পর্যন্ত যেখানে-যেখানে কর্তব্য কর্ম করিতে হয়, উহাকে এখানে (=এই বেদভাষ্যে) বিস্তার দ্বারা বর্ণন করেনি। কেননা কর্মকা-ের অনুষ্ঠানকে ঐতরেয়, শতপথ আদি ব্রাহ্মণ, পূর্বমীমাংসা আর শ্রৌতসূত্রাদি গ্রন্থে যথার্থ বিনিয়োগ করিয়াছেন। উহাকে পুনঃ কথন দ্বারা অনার্ষ গ্রন্থের ন্যায় পুনরুক্তি আর পিষ্টপেষণ দোষকে প্রাপ্তি হইয়া থাকেন।
এই প্রকার বেদার্থের বিষয়ে কিছু বেদে প্রতিপাদিত অতীন্দ্রিয়, অতিসূক্ষ্ম সৃষ্টি-বিজ্ঞানের প্রতিপাদক হইয়া থাকেন ।
কালান্তরে সমান নিবাস স্থানশীল (দ্যাবাপৃথিবী) পৃথক হয়। ইহার পৃথকতা বা দূরস্থ সূর্য আকাশে প্রকাশিত হয়। ইহার বর্ণন এই সামবেদের মন্ত্রে করিয়াছেন—-
অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি ৰর্হিষি।। (সাম০ ০১)
এই মন্ত্রে আসা-অগ্ন আয়াহি বীতয়ে-ইতি ইমো লোকো ব্যৈতাম্। অগ্ন আয়াহিইতি য়দাহঅনয়োলোংকয়োবীন্তয়ে। (তৈ০ স০ ৫.১.৫)
এই বীতয়ে পদের গম্ভীর মনোজ্ঞ এবং বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শাখা আর ব্রাহ্মণ গ্রন্থে করিয়াছেন। পূর্বাবস্থাতে সূর্য আর পৃথিবীলোক পৃথক পৃথক ছিল না। অগ্নিই তাঁহা পৃথক করিয়াছেন। অতঃ তৈত্তিরীয় শাখায় এই অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ইহা উভয় লোককে পৃথক করিবার জন্য কহিয়াছেন। যজ্ঞবাল্ক্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন—-
অগ্ন আয়াহি বীতয়ে ইতি। তদ্বেতি ভবতি বীতয়ে ইতি সমন্তকমিব হ বা ইমে অগ্রে লোকা আসুরিতি উন্মৃশ্যা হৈব দ্যৌরাস ইতি। (শ০ ব্রা০ ১.৪.১.৭)
অর্থাৎ হে অগ্নি! এসো [দ্যাবাপৃথিবীকে] দূর (=নিকটে নয় এমন স্থান) করিবার জন্য। বীতয়ে দ্বারা দূর হইবার অর্থ কহিয়াছেন। আরম্ভ (=উৎপত্তিকালে) এই লোক সমীপ (=পাশাপাশি-কাছাকাছি) ছিল। দ্যুলোক স্পর্শের যোগ্য ছিল।
এই মন্ত্রে দ্যাবাপৃথিবীর দূরত্ব অগ্নির কারণেই হইয়াছেন, ঐরূপ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বর্তমান আর পৃথিবী এই উভয়কে পৃথক হইবারÑইমৌ লোকৌ সহ সন্তৌ ব্যৈতাম্ এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বচন দ্বারাও বিদিত হইয়া থাকেন।
সূর্যকে দ্যু অর্থাৎ আকাশে স্থাপিত বর্ণন অনেক মন্ত্রে প্রাপ্ত হয়। যেরূপ—-
ইন্দ্রো দীর্ঘায় চক্ষসে আসূর্য় রোহয়দ্ দিবি। (ঋ০ ১.৭.২) অর্থাৎ ইন্দ্রই বিস্তৃত প্রকাশের জন্য সূর্যকে দ্যুলোকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন।
সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব হইবার পর মধ্যে অন্তরিক্ষ বৃদ্ধি হয়। যেরূপ নি¤œ মন্ত্রে এই তত্ত্বের কথন করিয়াছেন—-
য়ত্তে দিবি বর্চঃ পৃথিব্যাং য়দোষধীষ¦প্স¦া য়জত্র। য়েনন্তরিক্ষমুর্বাততন্থ ত্বেষঃ স ভানুরর্ণবো নৃচক্ষাঃ।। (ঋ০ ৩.২২.২) অর্থাৎ হে অগ্নি! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে রহিয়াছেন আর ওষধিতে বা জলে যজনীয় অংশ, যাঁহা হইতে এই অন্তরিক্ষ বিস্তৃত
হইয়াছে, সেই প্রকাশরূপ অর্ণব (=সমুদ্র) প্রাণীদিগের দৃষ্টি দানকারী হন।
অগ্ন আ য়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি ৰর্হিষি।। (সাম০ ০১)
এই মন্ত্রে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ব্যাখ্যা করিয়াছেন দেখুনÑঋগে¦দাদিভাষ্য-ভূমিকা গণিত বিদ্যা বিষয় (মহোমাহোপাধ্যায় পণ্ডিত যুধিষ্ঠির মীমাংসকের সম্পাদনায় পৃ০ ১৬৯)—-
য়থা ‘একা ক্রিয়া দ্ব্যর্থকরী প্রসিদ্বা’ ইতি ন্যায়েন স্বরসঙ্কেতাঙ্কৈর্বীজগণিতমপি সাধ্যত ইতি বোধ্যম্।
ভাষার্থঃ—-(একা চ মে০) এই মন্ত্রে ইহা অভিপ্রায় হয় যে, অঙ্ক, বীজ আর রেখা ভেদ দ্বারা যে তিন প্রকারের গণিতবিদ্যা সিদ্ধ করেন, উহাতে প্রথম অঙ্ক (১) যে সংখ্যা আছে, তাঁহা দুইবার গণনা দ্বারা দুই বাচক হইয়া থাকে। যেরূপ ১+১=২। এইরূপই সামনে এক তথা একের সামনে দুই বা দুইয়ের সামনে এক আদি যোগ করা জানা উচিত। এই প্রকার একের সহিত তিন যোগ দ্বারা চার (৪) তথা তিন (৩) কে তিন (৩) এর সহিত যোগ দ্বারা (৬) অথবা তিনকে তিনের সহিত গুণ দ্বারা ৩ঢ৩=৯ হয়।
এই প্রকার চারের সহিত চার, পাঁচের সহিত পাঁচ, ছয়ের সহিত ছয়, আটের সহিত আট ইত্যাদি যোগ বা গুণ তথা সব মন্ত্রের আশয়কে বিস্তার দ্বারা সব গণিতবিদ্যা প্রাপ্ত হয়। যেরূপ পাঁচের সহিত পাঁচ (৫৫), তদ্রুপই পাঁচ পাঁচ ছয় ছয় (৫৫) (৬৬) ইত্যাদি জ্ঞান গ্রহণ করা উচিত।
এইরূপই এই মন্ত্রের অর্থকে সামনে যোজনার দ্বারা অঙ্কের অনেক প্রকারের গণিতবিদ্যা অবশ্য জানা উচিত। [আর এখানে মন্ত্রে অনেক চকারের পাঠ দ্বারা অনেকবিধ গণিতবিদ্যা হয়, এরূপ মনুষ্যের জানা উচিত]।
আর যাঁহা বেদের অঙ্ক জ্যোতিষশাস্ত্র কহিয়া থাকেন, উহাতেও এই প্রকার মন্ত্রের অভিপ্রায় দ্বারা গণিতবিদ্যা সিদ্ধ করেন।
আর অঙ্ক দ্বারা যে গণিতবিদ্যা প্রকাশিত হয়, তাঁহা নিশ্চিত সংখ্যাত পদার্থে যুক্তহইয়া থাকে। আর অজ্ঞাত পদার্থের সংখ্যা জানিবার জন্য যে বীজ গণিত হয়, তাঁহাও একা চ মে০ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপ (অ+ক) (অ+ক) (কস্ট) ইত্যাদি সঙ্কেত দ্বারা বের হয়। ইহাও বেদ দ্বারাই ঋষি-মুনিগণ প্রকাশিত করিতেন। (অগ্ন আ০) এই মন্ত্রের সঙ্কেত দ্বারাও বীজ গণিত প্রকাশিত হয়।
আপডেট চরিতেছে…………………………………..